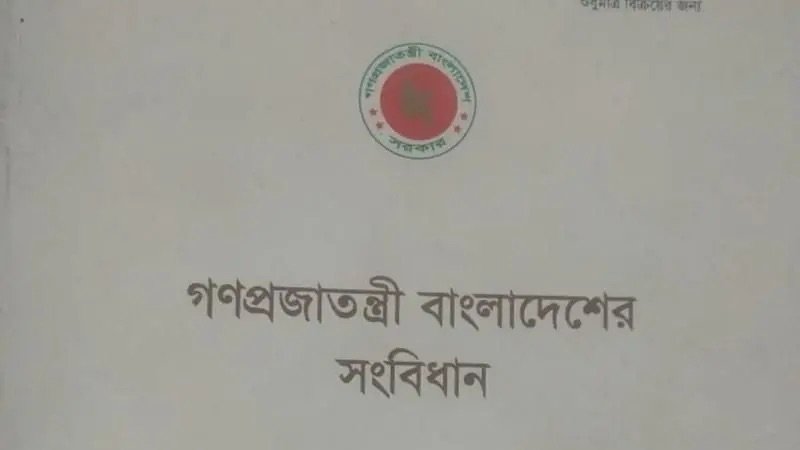বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত একাধিক সংস্কার কমিশন রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তনের পথে কাজ করছে।
গঠিত দশটি কমিশনের মধ্যে সংবিধান ও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।
এই প্রক্রিয়ায় সংবিধান পুনর্লিখনের দাবি উঠলেও, সংশোধনের মাধ্যমেই কাজ চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।
বিগত শেখ হাসিনা সরকারের আমলে শুরু হওয়া নানা বিতর্ক ও অস্থিরতা এই প্রক্রিয়ার পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে।
গণঅভ্যুত্থানের পর ক্ষমতাসীন অন্তর্বর্তী সরকার নতুন কমিশনগুলোকে দায়িত্ব দিয়ে রাষ্ট্রীয় কাঠামো পুনর্গঠনের পরিকল্পনা শুরু করেছে।
আলোচনার মূল বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমানো, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ চালু করা, এবং আনুপাতিক হারে ভোটের বিধান প্রবর্তন।
এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা একটি নতুন মোড় নিতে পারে।
সংবিধান সংস্কার: ক্ষমতার ভারসাম্যে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত
সংবিধান সংস্কার কমিশন ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব চূড়ান্ত করছে।
কমিশনের মতে, বর্তমান সংবিধান কোনো সরকারকে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে।
প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে সংবিধানে বড় ধরনের পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।
অংশীজনদের সাথে বৈঠকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রবর্তনের প্রস্তাব এসেছে।
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে সংবিধান সংশোধনের পরামর্শও এসেছে।
কিছু অংশীজন এক ব্যক্তিকে দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী না রাখার বিধান সংবিধানে যুক্ত করার সুপারিশ করেছেন।
পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিন ধরে চললেও, এই সংশোধনীর পরিবর্তন আনতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন বাড়ানো বা কমানো নিয়েও ভিন্ন ভিন্ন মতামত এসেছে।
কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, সব প্রস্তাবের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে কাজ করা হচ্ছে।
তবে সংবিধানের বিদ্যমান কাঠামোতেই এই পরিবর্তন আনা সম্ভব কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছে।
অনেকেই মনে করছেন, প্রস্তাবগুলো চূড়ান্ত করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ।
এদিকে, সাধারণ মানুষের মতামত সংগ্রহে অনলাইনে একটি প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছিল।
তবে সেখানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল অনেক কম।
গণপরিষদ গঠনের মাধ্যমে এই প্রস্তাবগুলোর অনুমোদনের কথাও কেউ কেউ বলছেন।
অন্যদিকে, বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী সংবিধান সংশোধনে সংসদের বাইরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।
প্রতিবেশী দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সংবিধান সংশোধনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।
তবে প্রক্রিয়াটি এখনও অনিশ্চয়তায় রয়েছে, কারণ রাজনৈতিক সমঝোতা ব্যতীত এই সংস্কারগুলো টেকসই হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।
নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার: সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ খোঁজা
নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে বেশ কয়েকটি সুপারিশ নিয়ে কাজ করছে সংশ্লিষ্ট কমিশন।
স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ইভিএম বাতিলের প্রস্তাব এসেছে।
স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার না করার সুপারিশও গুরুত্ব পেয়েছে।
নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইনে পরিবর্তন এনে আরও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া চালুর পরিকল্পনা করা হচ্ছে।
প্রবাসীদের ভোটাধিকারের বিধান চালু করতেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
সংবিধানে নির্ধারিত সীমানা পুনর্গঠন আইনে পরিবর্তনের প্রস্তাব এসেছে।
বিগত নির্বাচনগুলোর অনিয়ম এবং বিতর্কিত ইসির ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা হয়েছে।
এই প্রেক্ষাপটে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমে সরকারের হস্তক্ষেপ কমানোর জন্য আইনি সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে।
কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন, নতুন আইনে ইসির কার্যক্রম আরও স্বচ্ছ এবং গণতান্ত্রিক হবে।
তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও সংস্কার প্রয়োজন।
সংসদীয় নির্বাচনে স্বচ্ছতা আনতে, প্রার্থীদের আর্থিক লেনদেন এবং নির্বাচনী ব্যয়ের ওপর কঠোর নজরদারি সুপারিশ করা হচ্ছে।
গণঅভ্যুত্থানের পর মানুষের মধ্যে নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা পুনঃস্থাপন এখন বড় চ্যালেঞ্জ।
এক্ষেত্রে, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো দীর্ঘমেয়াদি সমাধান দিতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের সাথে বৈঠক করার জন্য ২২টি রাজনৈতিক দলের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে।
তবে, পুরনো আইন অনুযায়ী ইতিমধ্যে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন হওয়ায়, এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করে তা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে।
তবে রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া এই সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব হবে কি না, সেটিই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।
অর্থনৈতিক কাঠামোতে সংস্কার: আত্মনির্ভর অর্থনীতির স্বপ্ন
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার কমিশন আত্মনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে।
দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অনিয়ম দূর করাই কমিশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।
অর্থনৈতিক সংকটের পটভূমিতে ঋণনির্ভরতা কমানোর বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।
কমিশন কর কাঠামোর সংস্কারে একাধিক সুপারিশ প্রণয়ন করেছে।
প্রস্তাবিত পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে করপোরেট কর হার কমিয়ে ব্যবসার প্রসার ঘটানো।
অন্যান্য প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কৃষিখাতের জন্য বিশেষ প্রণোদনা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা।
দেশের ব্যাংকিং খাতের সংস্কার নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে।
কমিশন ব্যাংকের খেলাপি ঋণ কমাতে কঠোর আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেছে।
বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে লুটপাট রোধে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।
অনেকে মনে করছেন, এই সংস্কার উদ্যোগগুলো সফল হলে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়তে পারে।
অর্থনীতিবিদরা বলছেন, আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে রপ্তানি আয় বাড়ানোর পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
কমিশন রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণের সুপারিশ করেছে।
দেশের তৈরি পোশাক খাতের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আইটি এবং ওষুধ শিল্পের মতো খাতগুলোতে বিনিয়োগ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।
সরকারি ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ আরও স্বচ্ছ করার জন্য বিশেষ নিরীক্ষা প্রক্রিয়া চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
জ্বালানি খাতে ভর্তুকি কমানোর প্রস্তাবও আলোচনায় এসেছে।
তবে এই ভর্তুকি কমানোয় সাধারণ মানুষের ওপর এর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
দুর্নীতি রোধে কমিশন একটি স্বতন্ত্র ‘অর্থনৈতিক দুর্নীতি দমন ইউনিট’ গঠনের সুপারিশ করেছে।
এই সুপারিশের পেছনে রয়েছে টিআইবির প্রতিবেদনে উঠে আসা তথ্য, যা অনুযায়ী বাংলাদেশের সরকারি খাতে দুর্নীতি বাড়ছে।
অনেকেই মনে করছেন, সংস্কারের এই উদ্যোগগুলো দ্রুত বাস্তবায়িত হলে বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরতা কমবে।
কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, সংস্কার প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবে যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকে।
বিচারব্যবস্থার সংস্কার: আইনের শাসনে নতুন দিগন্ত
বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা সংস্কার কমিশন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।
দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া এবং মামলার জট দেশটির বিচারব্যবস্থার প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
কমিশন পুরনো এবং অপ্রয়োজনীয় আইনের তালিকা তৈরি করে তা বাতিল করার সুপারিশ করেছে।
তিন বছর ধরে চলমান মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত গঠনের প্রস্তাব এসেছে।
মানবাধিকার লঙ্ঘনের মামলা নিয়ে কমিশন একটি স্বাধীন ‘মানবাধিকার আদালত’ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে।
কমিশন বলছে, বিচারকদের প্রশিক্ষণ এবং বিচারিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করাই দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের মূল চাবিকাঠি।
পাশাপাশি, বিচারিক কাঠামোতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
অনলাইন মামলা দায়ের এবং ভার্চুয়াল আদালতের ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
কমিশনের প্রধান ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বলেছেন, এই প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়িত হলে মামলার জট অনেকাংশে কমবে।
দুর্নীতিগ্রস্ত আইনজীবীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ারও সুপারিশ করা হয়েছে।
আইনজীবীদের মধ্যে পেশাগত আচরণবিধি বাস্তবায়নে একটি স্বাধীন বোর্ড গঠনের প্রস্তাব এসেছে।
মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলো কার্যকর হলে মানুষের আইনি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে আস্থা বাড়বে।
তবে, আইনি সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক এবং প্রশাসনিক পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে।
এছাড়া, ভুক্তভোগীদের সুরক্ষায় আইনি সহায়তা তহবিল বাড়ানোর সুপারিশও গুরুত্ব পেয়েছে।
প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিচারপ্রক্রিয়া সহজ করতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিশেষত নারীরা হয়রানিমুক্ত আইনি সহায়তা পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিচারব্যবস্থা সংস্কার শুধু আইন ও বিচার ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল নয়।
এর জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং প্রশাসনিক সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বিচারিক সংস্কার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা চললেও, এটি বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি।
এদিকে, কিছু বিরোধী রাজনৈতিক দল কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।
সংস্কারের এই উদ্যোগগুলো সফল হলে, বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা দক্ষিণ এশিয়ায় একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।
সংস্কার বাস্তবায়নের পথে চ্যালেঞ্জ
চারটি খাতেই সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হলেও, চ্যালেঞ্জগুলোর কোনোটি সহজ নয়।
রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় বাধা বলে মনে করা হচ্ছে।
সংস্কার কমিশনগুলোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আসতে পারে।
তবে, এই প্রক্রিয়া সফল করতে জনগণের আস্থা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই সরকারের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।